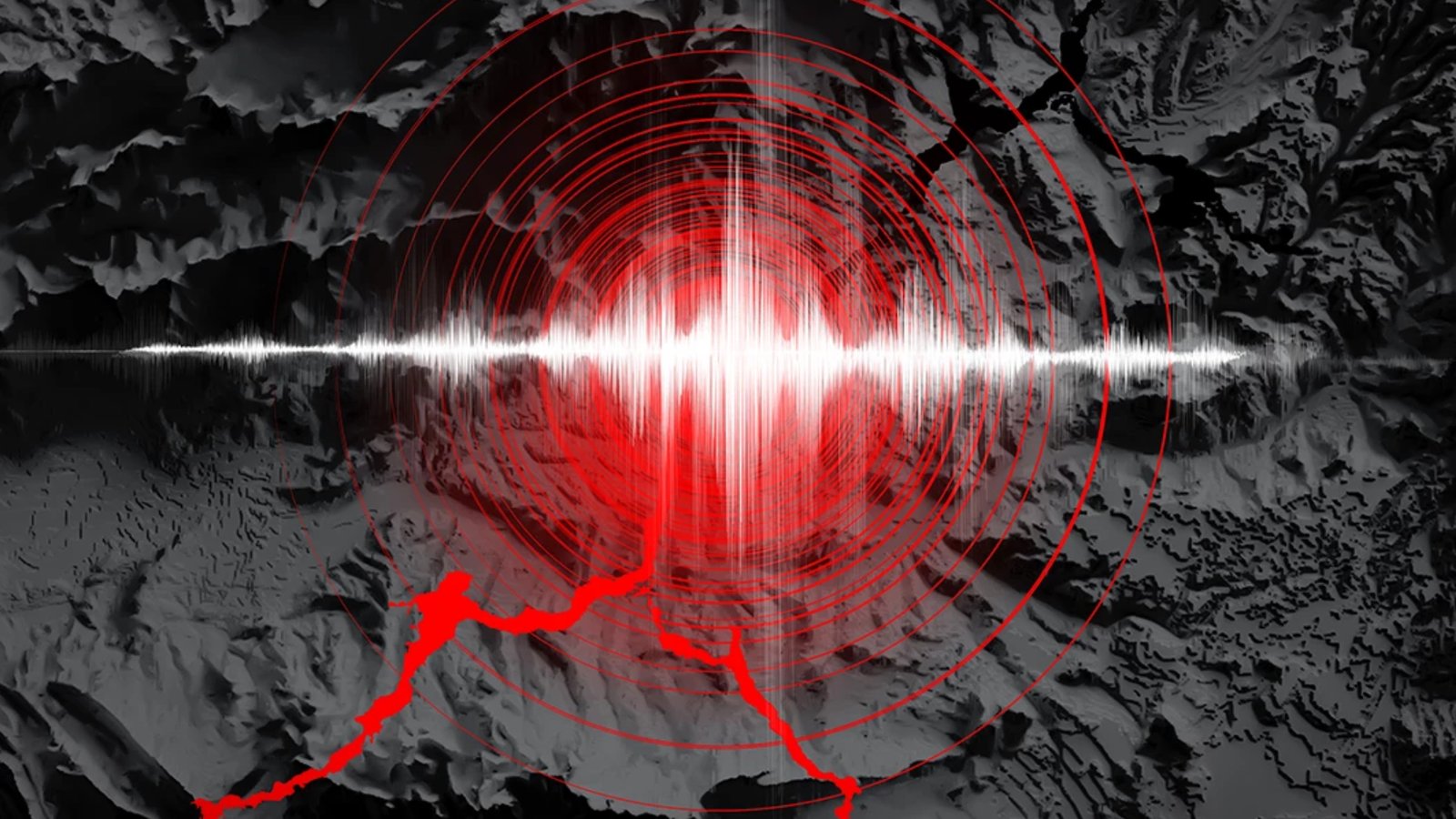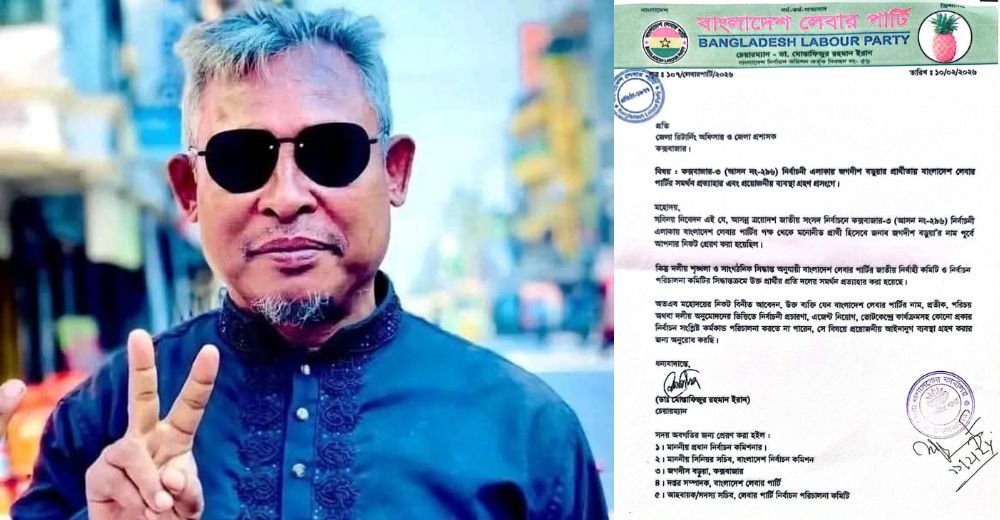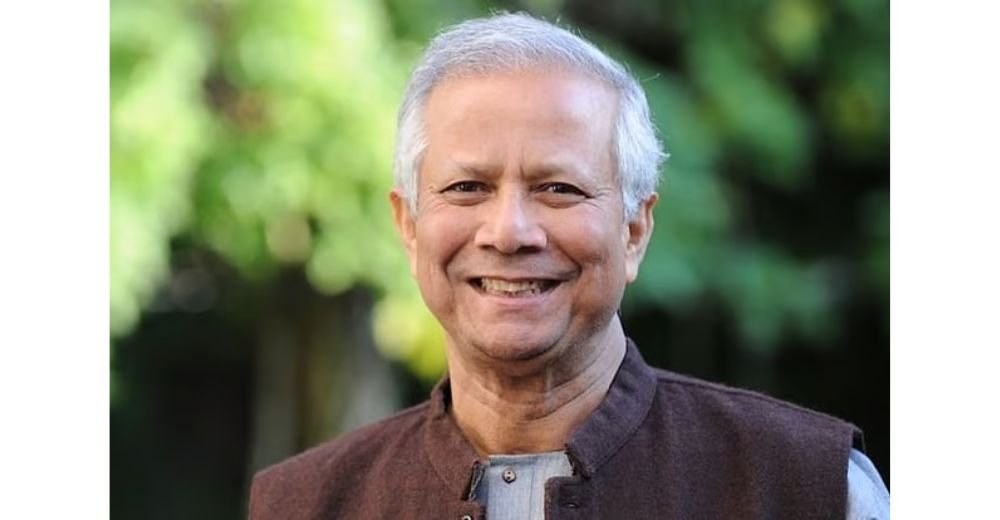মহালয়া মানেই অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করে আলোর আগমনী। পিতৃপক্ষের অবসান আর দেবীপক্ষের সূচনার সেতুবন্ধন এই ভোর। ভোররাতের আকাশে ধূপের গন্ধ, শঙ্খধ্বনি আর রেডিওতে মহালয়ার ভরাট কণ্ঠ মিলেমিশে তৈরি করে এক অনন্য আবেশ। মহালয়ার সকাল তাই বাঙালি হিন্দুদের আবেগ, ভক্তি আর শিকড়ের টানে মিশে আছে।
এ ভোরকে চিরস্মরণীয় করে তোলেন এক মানুষ—বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর কণ্ঠে মহালয়া ছাড়া যেন এ সকাল অসম্পূর্ণ।
তবে ১৯৭৬ সালের সেই ভোর ছিল অন্যরকম। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ভেসে এল মহানায়ক উত্তম কুমারের কণ্ঠ। সঙ্গে ছিল জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা শিল্পী লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলের গান। নতুন নাম দেওয়া হলো—“দেবীং দুর্গতিহারিণীম।” সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুন্দরভাবে রেকর্ডিং হলেও ভদ্রের কণ্ঠে অভ্যস্ত বাঙালি তা মেনে নিতে পারল না। একের পর এক ফোন আসতে লাগল রেডিও দপ্তরে, ডাকবাক্স ভরে গেল অভিযোগে। রেডিও অফিসের জানালা ভাঙল জনরোষে, রাস্তায় দেখা গেল ভাঙা রেডিওর স্তূপ।
অবশেষে রেডিও স্টেশনের কর্তারা ভুল বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন বাঙালি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছাড়া আর কাউকেই এই জায়গায় বসাতে পারবে না। হোক সেটি মহানায়ক উত্তম কুমার। তাই ষষ্ঠীর দিন ভোরে রেডিওতে আবার ভেসে এল চেনা সেই কণ্ঠ—
“আশ্বিনের শারদপ্রাতে,
বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর,
ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা,
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা,
আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নব ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন।”
এই আবির্ভাবেই শান্ত হলো জনরোষ। বাঙালি ফিরে পেল তার চিরচেনা মহালয়া।
১৯৩০ সালে প্রথম চণ্ডীপাঠ শুরু করেছিলেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। তখনও সমালোচনা হয়েছিল—কারণ তিনি ব্রাহ্মণ নন। শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন—“আমি পাঠ করি না, পুজো করি।” আজ সেই সমালোচকরা ইতিহাসে মিলিয়ে গেছেন, অথচ তাঁর কণ্ঠ আজও অমলিন।
আজও তাই সনাতনীদের ঘরে ঘরে ভোরবেলা শোনা যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক—
“যা চণ্ডী, মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী, যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী ।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভ-দৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।”
এই আবহ ছাড়া যেন দেবীপক্ষের সূচনা অসম্পূর্ণ।
শ্রদ্ধা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রকে—যাঁর কণ্ঠ ছাড়া সনাতনীদের মহালয়ার সকাল ভাবাই যায় না।

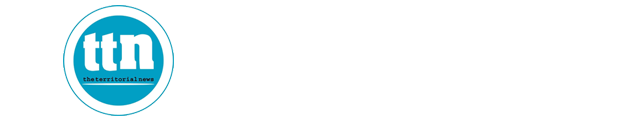
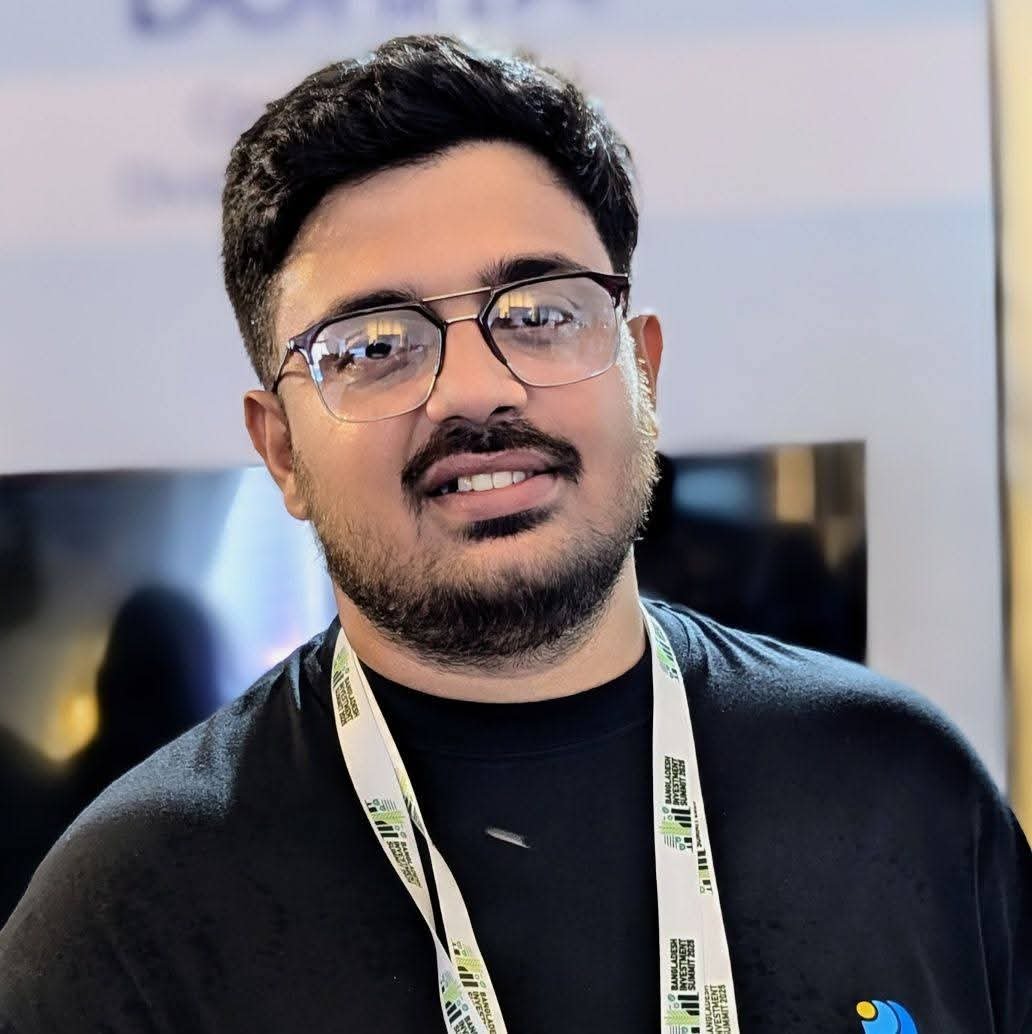 সায়ন্তন ভট্টাচার্যের ফিচার-
সায়ন্তন ভট্টাচার্যের ফিচার-