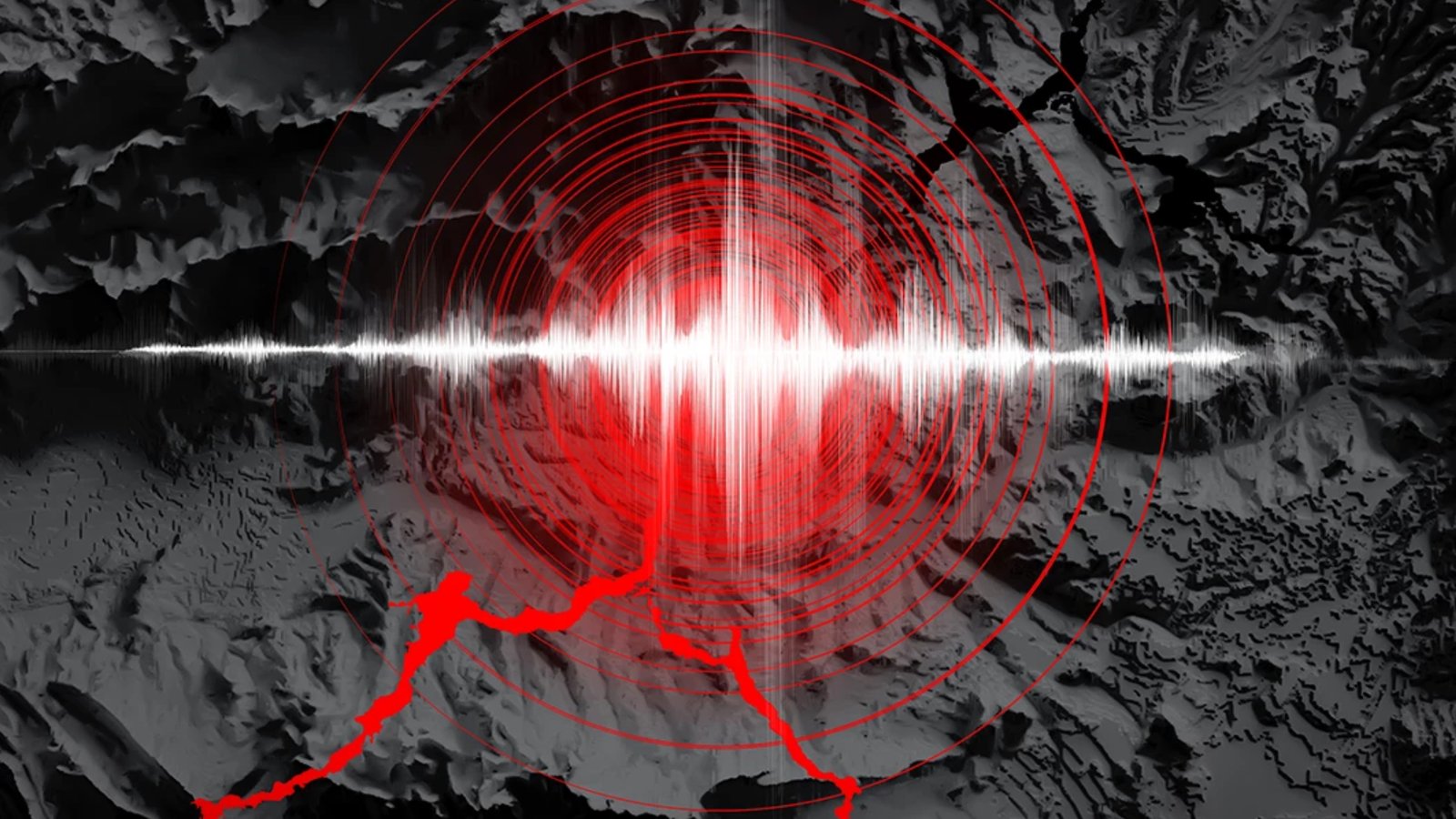রাজশাহীর তাহেরপুরের প্রাচীন জনপদে শরৎকালের সোনালি আলো মাখা এক দুপুর। মাঠে বাজল ঢাক, শিউলির গন্ধে ভরে উঠল চারপাশ। ইতিহাসের পাতায় সেদিন লেখা হলো এক নতুন অধ্যায়; বাংলার প্রথম রাজকীয় দুর্গাপূজা। আর সেই আয়োজনের পেছনে ছিলেন জমিদার রাজা কংসনারায়ণ।
তার আগে দুর্গাপূজা ছিল নিভৃত ঘরের আচার, পরিবারের ভক্তির সীমাবদ্ধতা। কিন্তু রাজা কংসনারায়ণ ভেবেছিলেন ভিন্ন কিছু। তিনি চেয়েছিলেন দেবীর পূজা হবে শুধু ভক্তির নয়, হবে এক মহা-সম্মিলন, যেখানে প্রজা আর জমিদার একই উৎসবে মিশে যাবে। ১৫৮০ সালের দিকে তার প্রাসাদের আঙিনায় প্রথম সেই মহোৎসব বসে। ঢাকের শব্দে প্রজাদের মুখে ফুটে ওঠে আনন্দ, মেলায় জমে ওঠে বেচাকেনা, আর সমাজ পায় এক নতুন ঐক্যের সেতুবন্ধন।
রাজা মনে করতেন, পূজা মানেই শুধু দেবী আরাধনা নয়; এটি মানুষকে কাছাকাছি আনার শক্তি। শরতের পূর্ণিমায় মা দুর্গার আগমন হলো প্রজাদের কাছে আনন্দ, আশ্রয় আর ভরসার প্রতীক। দেবী যেন কেবল দেবী নন, কন্যা, যিনি বছরে একবার বাপের বাড়ি আসেন। আর বিদায়ের দিন বিসর্জনে ভিজে ওঠে চোখ, শেখায় অনিত্যতার পাঠ, তবুও বুক ভরে থাকে আগামী বছরের স্বপ্নে।
আজও বাংলার দুর্গাপূজা সেই উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে। শিউলি, কাশফুল, আর ঢাকের তালে যখন মা আসেন, তখনো মনে পড়ে সেই প্রাচীন তাহেরপুর। যেখানে রাজা কংসনারায়ণ প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন, এক পূজা, যা সমাজকে গাঁথবে ভালোবাসা আর ঐক্যের অটুট সুতায়।
চার শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। তবু আজও দুর্গাপূজা মানে শুধু ধর্ম নয়, মানে ভালোবাসার উৎসব, সমাজের বন্ধন আর মানুষের অনন্ত স্বপ্ন।
লেখক: শেখ জাহাঙ্গীর হাছান মানিক , চিন্তক ও গবেষক।

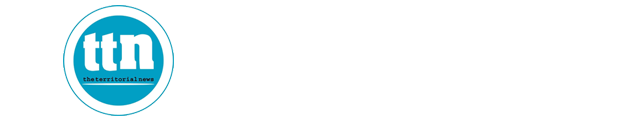
 শেখ জাহাঙ্গীর হাছান মানিক
শেখ জাহাঙ্গীর হাছান মানিক